
কালক্রমে বদেশ্বরী মন্দিরের নামানুসারে এ এলাকার নাম হয় বোদা!!
বিস্তারিত: বিগত চারশত বছরে নানান চরাই–উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে আজকের বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে বোদা পরগণার অবস্থান। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে মীরজুমলার এ অঞ্চলে আগমনের নানান চিহ্ন আজো বলবৎ। মোগলি–কেল্লা, নয়নীবুরুজ আজও মীরজুমলার আগমনের বার্তা বহন করে। বিগত আড়াইশত বছরে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল এ পরগণা। কোন কোন বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পরে উত্তাপ ছড়িয়েছিল এ পরগণার বাইরেও। আর এ অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে অনেক আগেই। ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী ব্যাপক কোন আন্দোলন না হলেও কৃষক বিদ্রোহ, সাওতাল বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, হাজী শরীয়তুল্ল্যাহর আন্দোলন, দুদু মিয়ার আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। আর এ পরগণায় কৃষক বিদ্রোহ, ফকির–সন্ন্যাস বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন ব্যাপকতা ছড়ায়, যার উত্তাপ পরগণার বাইরেও পড়ে।
এ জেলার জনপ্রবাহের মধ্যে রয়েছে–হিন্দু ও মুসলমান প্রধান ধারা, এছাড়াও রাজবংশী, কোচ, পলিয়া, সাঁওতাল, ওঁরাও, হাড়ি, ভূইমাল, কামার–কুমার, বেহারা, কাহার, সুনরী, বয়াতী, পাঠান, শেখ প্রভৃতি। এই বিচিত্র জনধারার মিশ্র রুপায়নেই গড়ে উঠেছে বোদা পরগণার নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি। “বোডো” ভাষা গোষ্ঠী বা মঙ্গোলীয় নর গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোচ, রাজবংশী, পলিয়া ইত্যাদি জাতির একটি প্রধান ধারা এ পরগণায় পরিলক্ষিত হয়। এদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপ : নাক মধ্যমাকৃতি থেকে চ্যাপ্টা, মাথার আকৃতি সাধারনত গোল, অক্ষিপট সম্মুখীন, উন্নত গন্ডাস্থি, কেশবিহীন দেহ ও মুখমন্ডল, সোজা চুল, বিরল দাড়ি–গোঁফ, পায়ের রং পীতাভ অথবা বাদামী পীতাভ। এই জনগোষ্ঠী অতি প্রাচীন কালে দক্ষিন পশ্চিম চীন হতে ক্রমশ বঙ্গদেশ, মালয় উপদ্বীপ এবং পূর্ব দক্ষিন সমুদ্র উপকূলীয় দেশ এবং দ্বীপগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। পথে উত্তর আসামে এবং ব্রক্ষ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বোডো বা মেচ সম্প্রদায় ভূক্ত কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকের মধ্যে একটি ধারা প্রবাহ ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে এসে ঢুকে পড়ে। রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এভাবেই খানিকটা মঙ্গোলীয় প্রভাব সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের রক্তে আত্মপ্রকাশ করেছে। বোদা পরগণার কোচ, পলিয়া, রাজবংশী জনগোষ্ঠী উল্লিখিত জনপ্রবাহের উত্তরসূরী।
বোদা পরগণার ইতিহাস অতি প্রাচীন। এর নাম করনেও অনেক মতভেদ রয়েছে মনে করা হয়, অতি প্রাচীনকালে করতোয়া নদী অনেক খর¯্রােতা ও বৃহৎ আকারে অত্র অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহমান ছিল। কথিত আছে সতী বা পার্বতী দেহ ত্যাগ করলে তার দেহের বিভিন্ন অংশ অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের একান্নটি স্থানে পতিত হয়। দেহের অংশগুলি যে যে স্থানে পতিত হয় সে স্থানগুলি পীঠস্থান হিসাবে স্বীকৃত হয়। সতীর বাম পায়ের গোড়ালী বোদা এলাকার করতোয়া নদীতটে পতিত হয়। সতীদেহ যেহেতু গহীন অরণ্যে পড়েছে তাই সুবিধাজনক জায়গায় তার একটু পার্শ্বেই একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এই স্থানটি বদেশ্বরী নামে পরিচিত। পূর্ণ্যস্থানে তদানীন্তন কোচ রাজা প্রাণ নারায়ন বদ্বেশ্বরী মন্দির নির্মাণ করেন।
কালক্রমে বদেশ্বরী মন্দিরের নামানুসারে এ এলাকার নাম হয় বোদা।
এছাড়া জানা যায় যে, মোঘল শাসন আমলে শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাকে কতগুলো পরগণা বা চাকলায় বিভক্ত করা হয়। কুচবিহার মহারাজার রাজত্ব ছিল উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে, পূর্বে পাটগ্রাম, দক্ষিনে বোদা দেবীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃতি। চাকলার অভ্যন্তরের জমিদারির নামকরণ করা হয় চাকলাজাত এস্টেট। কুচবিহার মহারাজার চাকলাজাত এস্টেটের হেড অফিস ছিল বোদায়। এখান থেকেই খাজনা আদায়ের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। খাজনা আদায়ের প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হতো নায়েব। বোদা চাকলার কর্মরত নায়েবের নাম ছিল বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ নায়েব মহাশয় সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পালকিতে চলাফেরা করতেন। জনশ্রুতি আছে নায়েব বৈদ্যনাথকে সংক্ষেপে বৈদ্য বলে ডাকা হতো। কাল ক্রমে বৈদ্য শব্দ থেকে বোদা নামের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। ডঃ বুকানন হেমিল্টনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, এই অঞ্চল খুবই উন্নত ছিল। বন্দর হিসাবে এ অঞ্চল খ্যাত ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, বন্দর থেকে বোদা নামের উৎপত্তি। আবার সাম্প্রতিক কালে আলোচনা উঠেছে যে, “বোডো” ভাষাগোষ্ঠী থেকেই বোদা নামের উৎপত্তি। কারন বর্তমান পঞ্চগড় শহরের পার্শ্বেই একটি পাড়ার নাম “বোদা পাড়া”।
ছিয়াত্তরের মন্বত্ত্বরের (১৭৭০খ্রী) ফলে এ অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক লোক মারা যায়। লোকবলের অভাবে সে সময় কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এ দূর্যোগের মধ্যে সরকারীভাবে ভুমি রাজস্বের পরিমান বৃদ্ধি করা হয়। জমিদার দেবীসিংহ বাড়তি রাজস্ব আদায়ের জন্য কৃষকদের উপর বল প্রয়োগ শুরু করেন। প্রতিবাদে কৃষকরা জেলা কালেক্টরের স্মরনাপন্ন হলে তিনি নির্বিকার ছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকরা ১৭৮৩ খ্রিঃ সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। কৃষকদের আক্রমনের ফলে দেবীসিংহের গোমস্তারা পলায়ন করে। এসময় কয়েকজন কর্মচারী আহত–নিহত হন। তারা ক্রমে ব্রিটিশ সরকারকে অমান্য করতে আরম্ভ করে। সরকার এ অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করতে শেষমেষ সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। এ অঞ্চলে সংগ্রাম করতে গিয়ে বহু কৃষক আহত–নিহত হন এবং অঞ্চলের কৃষকদের চাপেই সরকার দেবীসিংহকে আটক করে এবং ভূমি রাজস্ব হ্রাস করা হয়। অত্র অঞ্চলে কোন প্রশাসনিক ইউনিট না থাকায় এবং এলাকাটি ঘনঅরণ্য বেষ্টিত হওয়ার কারনে বৃটিশ সরকার কৃষক বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয় এবং এ এলাকায় কোন নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কৃষক বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হওয়ায় এবং এলাকায় বৃট্রিশ সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার একটি প্রশাসনিক ইউনিট সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই ১৭৯৭ সালে বোদা থানার গোড়াপত্তন শুরু হয়।
১৭৭০–১৮৬৮ পর্যন্ত বোদা পরগনা রংপুর জেলার অধীনে ছিল। ১৮৬৯ –১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বোদা ছিল জলপাইগুড়ি জেলার অধীন। কুচবিহার প্রশাসন, বোদা থানা প্রদত্ত সম্পত্তি রেট ফি হিসেবে বোদা থানাকে দান করে ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ তারিখে একটি আদেশ জারি করেন। আদেশটি ০৯/০১/১৯৮৪ তারিখে কলকাতা প্রথম খন্ডের ১৭৭ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।
জলপাইগুড়ি জেলার অধীন তিনটি থানা ছিল (১) জলপাইগুড়ি সদর (২)রাজগঞ্জ(৩) বোদা। বোদা ছিল জলপাইগুড়ি জেলার বৃহত্তম থানা। বোদা থানার অধীন দুইটি পুলিশ আউট পোষ্ট ছিল। একটি পঞ্চগড়ের উত্তরে জগদল এবং অপরটি করতোয়া নদীর পূর্ব পাড়ে দেবীগঞ্জ। কালক্রমে দেবীগঞ্জ এবং জগদল পূর্ণাঙ্গ থানায় রুপান্তরিত হয়। জগদল হতে থানাটি পরবর্তীকালে পঞ্চগড় ( বর্তমানস্থানে) স্থানান্তর করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর দিনাজপুর জেলা, ঠাকুরগাঁও মহকমুার নিয়ন্ত্রণে আসে। বর্তমানে এ অঞ্চলটি পঞ্চগড় জেলার অধীন। বর্তমানে এই অঞ্চলের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগন মুসলমান। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এ অঞ্চলে যত হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে। এ পরগণায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বাস এখনও আছে। আর সাঁওতাল জনগোষ্ঠী তাদের আদি কৃষ্টিকে স্বযতেœ লালন করে আসছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেলে বিপর্যস্ত বহু সিপাহী এপরগণায় পালিয়ে আসে। ঐ সমস্ত সিপাহী তেঁতুলিয়া সংলগ্ন ঘন জঙ্গলসহ নেপাল–ভূটান পর্যন্ত অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং আত্মগোপন করে থাকেন। “ফাঁসিদেওয়া” নামক স্থানে সিপাহীদের ফাসিঁ দেওয়া হয়। ফাসিঁদেওয়া, সিপাহীপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সিপাহী বিপ্লবের স্মৃতিবহ। এই জনপদে ফকির মজনু শাহ, ভবানী পাঠক প্রভৃতি ফকির ও সন্ন্যাসী নেতার নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়। সন্ন্যাসী কাটা, সন্ন্যাসী পাড়া, দেবীগঞ্জ,দেবীডোবা প্রভৃতি অঞ্চলের নামকরণ সেই স্মৃতিকে ধারন করেই করা হয়েছে। সন্ন্যাসী কাটায় ধৃত সন্ন্যাসীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। ফকির ও সন্ন্যাসী বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী অনেক ফকির ও সন্ন্যাসীও এ অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। সে কারনে এ অঞ্চলের অনেক গুলো পাড়ার নাম ফকির পাড়া। এছাড়া ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর জলপাইগুড়ি জেলা থেকে এবং ১৯৫৩ সাল থেকে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী, পাবনা, ঢাকা, ও ময়মনসিংহের বিপুল সংখ্যক মানুষ পঞ্চগড় জেলায় এসে স্থায়ীভাবে থেকে যান। উল্লিখিত জনপ্রবাহ ধীরে ধীরে স্থানীয় জনধারার সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলেন। বহিরাগত এই জনপ্রবাহের মধ্যে ছিল অ্যালপাইন, মঙ্গোলীয়,দ্রাবিড়, আদি– অস্ট্রেলীয় প্রভৃতি মিশ্র উপাদান। পঞ্চগড় জেলার নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য বিনির্মানে এদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।
রাজনৈতিক:
পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে এ অঞ্চলের মানুষ রাজনৈতিক ভাবে একেবারেই সচেতন ছিল না। শিক্ষা–দীক্ষায়ও গোটা ভারত বর্ষের মধ্যে ছিল পিছিয়ে । পলাশীর যুদ্ধের পরে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন শুরু হয়। দেশ জাতি, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি সর্ম্পকে জনগণ সচেতন ছিলনা। ধর্ম বিশ্বাস কিংবা ধর্ম ভিত্তিক আচার–অনুষ্ঠান ছিল তাদের
সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তি। পীর, ফকির, সন্ন্যাসী, যোগিরা ছিলেন জনগনের আধ্যতিœক নেতা। লাখেরাজ, দান ও ধর্মীয় জীবনের অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকতেন। এই অঞ্চলের জনগন এবং নেতাদের দেশী বিদেশী সরকার নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা ছিলনা। কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই অঞ্চলের জন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসক গোষ্ঠী হস্তক্ষেপ করতে চাইত। দ্বৈত শাসন এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তÍর এর কারনে এ অঞ্চলে অরাজকতা শুরু হয়। এ অঞ্চলের মানুষ সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি। তারা বুঝতে পারে উদ্ভুত পরিস্থিতির মুল হোতা ইংরেজ। এ এলাকার মানুষ সরকারী নীতির প্রতিরোধ করতে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে এগিয়ে আসে। গোটা দেশের মতো এ অঞ্চলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিরোধ অন্দোলনে অগ্রসর হয়। বোদা শহরকে মধ্যযুগে অভিহিত করা হতো নগরকুমারী নামে। সুতরাং এখানে নগর শব্দটি ব্যবহার হয়েছে বন্দর অর্থে । সম্ভবত কোন সৌখিন ও সংস্কৃতি প্রিয় ব্যক্তি কুমারী মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে এর নাম করণ করেছিলেন। বস্তুত এই নগরটি ছিল অতি চমৎকার। ডা. বুকানন হেমিল্টন ১৮০৯ খ্রিষ্টাদ্বে এই অঞ্চল পরিদর্শন করে জানিয়েছিলেন, বোদায় কুমারী কোর্ট (নগরকুমারী) নামক একটি ছোট শহর বিদ্যমান ছিল। সেখানে বসবাস করতেন দেশীয় কর্মকর্তাগণ ও পুলিশ অফিসারগণ। এখানকার বাড়ীঘর গুলো উন্নতমানের। কোচ বিহারের মহারাজার কর্মচারীগণও এই নগরে বসবাস করতেন। ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে নগরকুমারীতে বাড়ী ঘরের সংখ্যা ছিল ২০০ দুই (শত) টি। নগরকুমারী নিকর্টবর্তী ভাসাই নগর গ্রামে এককালে বসবাস করতেন বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ । সম্ভবত এই গ্রামে গড়ে উঠেছিল উপ শহর । অঞ্চলটি পাথরাজ নদীর বন্যায় প্লাবিত হয়ে ভাসাই নগর নামধারন করেছিল বলে অনুমিত হয়।
১৭৭৭ সনে জয়সিংহকে বোদা পরগণার তিন আনার চৌধুরী নিযুক্ত করা হয়। ১৭৭৭–৭৮ খ্রিঃ রাজার চাকলাজাত এই অঞ্চলের জমিদারীর দায়িত্ব অর্পিত হয় নাজির খগেন্দ্র নারায়নের নামে তার দেওয়ান রাম চন্দ্র এবং তার পুত্র শ্যাম চন্দ্রের উপর। কিন্তু তারা আদায়কৃত রাজস্বের প্রায় সমস্তই আত্মসাৎ করতেন। সামান্য কিছু প্রদান করেতেন নাজিরকে। পক্ষান্তরে রাজাকে কিছুই দেওয়া হতো না। এ সময় ফকির চন্দা ও হরি নারায়ন ছিলেন বোদা চাকলার চৌধুরী, তারা নিজেরাই ভিন্ন ভিন্ন পরগনার জমিদার হওয়ার প্রত্যাশায় “স্বত্বেরদাবী” তুলে রংপুরের কালেকটরের নিকট মহারাজা ও নাজিরের নামে মামলা দায়ের করে। সেই মামলার রায়ে কালেকটর মি. পার্লিং সিন্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, চৌধুরী গণ এবং নাজির ‘‘চাকলা বোদার’’ কর্মচারী মাত্র। কোচ বিহারের মহারাজাই চাকলা বোদার প্রকৃত অধিকারী । ১৭৭৮ সনে পরিচালিত হয় এই মামলা । বোদা চাকলার উপর মোঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (১৭১১ খ্রিঃ) ৫৪ বছর পর ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী লাভ করেন দেওয়ানী। ১৭৭০ খ্রিঃ মি. গ্রোস নিযুক্ত হন রংপুর অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের সুপারভাইজার । কিছু দিনের মধ্যে কোম্পানী রংপুর কে জেলা হিসাবে গড়ে তুলেন, যার মধ্যে অর্šÍভূক্ত বোদা পরগনাটি । মি. গ্রোসের অব্যবহিত পূর্বে বোদা চাকলার রাজস্ব সংগ্রাহক ছিলেন মির্জা হোসেন রাজা এবং মদন গোপাল। মি. গ্রোসের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত নাজির ছিলেন বোদা চাকলার সর্বময় কর্তা । তিনি কোম্পানীর নিকট আজ্ঞাবহ ছিলেন না। মি. গ্রোস কালেকটর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বোদা চাকলার কোন জমিদার কোম্পানী কর্তৃক ধার্যকৃত রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে তার জমিদারী অন্য কোন ঠিকা বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। কোম্পানীর শর্তযুক্ত জমিদারী কোচ বিহার মহারাজারা মানতে চাইতনা। তাই মহারাজার সাথে কোম্পানীর বিরোধ শুরু হয়। কোচবিহার মহারাজা উপেন্দ্র নারায়ন ১৭৩৭–৩৮ খ্রিঃ ভুটানের রাজার সহায়তায় মোঘলদের পরাজিত করে নিজ সিংহাসন উদ্ধার করেন। ভুটান রাজের সাহায্য গ্রহণের ফলে বোদা পরগনায় ভুিটয়াদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। অতপর এই অঞ্চলে শুরু হয় নানা রুপ অশান্তি । এ পরগনার “নয়নীবুরুজ” তাদের স্মৃতি বিজরিত স্থান।
ভুটানিরা এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, কোচ বিহারের একজন রাজাকে আটকে রেখেছিল ভুটানে। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী একাধিক বার ভুটান সীমান্তে সৈন্য প্রেরণ করে কিন্তু তারা ফিরে আসে পরাজিত হয়ে। তাদের সংঙ্গে কোম্পানী স্বাক্ষর করেন একাধিক সন্ধি। ভুটানিদের জন্যই কোম্পানী এ পরগনায় সেনাবাহিনী নামান। সর্বশেষ ১৮৬৪ সালে কোম্পানী ভুটান দুয়ার বা সীমান্ত অধিকারের ঘোষণা দেন। ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি প্রহণ পূর্বক শুরু করে সর্বাত্বক যুদ্ধ। এবারে চুড়ান্ত ভাবে বিজয়ী হয় ব্রিটিশ বাহিনী ।
ব্রিটিশ–ভুটান যুুদ্ধে কোম্পানীকে সহায়তা করেন বোদা পরগনার চন্দনবাড়ী গ্রামের তরিকুল্লাহ্। কোম্পানী তাকে পুরস্কার হিসাবে প্রদান করেন বহু ভু–সম্পদ এবং বোদা চাকলার দায়িত্বপূর্ণ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ। তরিকুল্লাহ্র নামের প্রথম বর্ণ ঞ হওয়ায় পরবর্তী কালে তার পরিবার পরিচিতি লাভ করে টি ফ্যামিলি হিসেবে। এই পরিবারের বিখ্যাত কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খান বাহাদুর তসকিমউদ্দীন আহম্মদ এবং কলকাতা মোহামেডান স্পোটির্ং ক্লাবের বিখ্যাত গোলরক্ষক তছলিমউদ্দীন আহম্মদ। টি ফ্যামিলির প্রথম পুরুষ মুন্সি তরিকুল্লাহ বৃটিশ বাহিনীর মেজর ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বোদা বেঞ্চ কোর্টের প্রথম বিচারক ছিলেন। বিচার কার্য পরিচালনার জন্য সেই সময় অবিভক্ত বাংলার অনেক নামি দামী উকিল মোক্তার বোদায় আগমন করেন। তাদের কেউ কেউ এ অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন।
জীবন যাত্রা:
এই অঞ্চলের মানুষের বসতির কথা জানা যায় সেই বৈদিকযুগ হতেই। প্রকৃতির যে একটা নিয়ম ও পরিবর্তন চলছে সেটা এই অঞ্চলের দিকে তাকালেই বুঝা যায়। এই অঞ্চলের যে কোন বয়স্ক মানুষের সাথে কথা বললেই জানা যায় যে, এখন যেখানে তার বাড়ী ও আবাদী জমি, তাঁর শৈশব ও কৈশরে তিনি সেখানে দেখেছেন, বাঘ, হরিণ আর শিয়ালের বসবাসের জন্য জঙ্গল। এই অঞ্চলের মানুষের ঘরবাড়ী ছিল প্রাচীন কাল হতেই কাঠ ও বাঁশের খুটির উপরে ছন বা খড়ের ঘর, বাড়ীর পার্শ্বে থাকত বাঁশঝাড়, বিত্তবানদের বাড়ীর সাথে পুকুর, নিম্নবিত্তদের ডোবা, সেখানে মাছের চাষ করত। বংশানুক্রমিক ভাবে মানুষ দাদা বাবার ভিটা মাটি ছাড়তনা, সেখানেই বসবাস করত। এছাড়াও মাটির ঘর যাকে কোঠার ঘর বলতো, সেই ঘরেরও প্রচলন ছিল এ এলাকায়। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে খোলতায় থাকতো বৈঠকখানা। ঘর, আঙ্গিনা, দরজা মাটি দিয়ে লেপা হতো। ড. বুকানন হেমিল্টন ১৮০৯ সালে বোদা পরগনায় পরিদর্শন করতে এসে একটিও পাকা বিল্ডিং দেখতে পাননি মানুষের বসবাসের জন্য। বড় বড় জোতদার, জমিরদারদের হয়ত ৬/৭ কুড়ে ঘর, রান্না ঘর আলাদা, আর সাধারণ মানুষের দুটো ঘরেই যথেষ্ট ছিল। সবাই বর্ষাকাল ব্যতিরেকে খোলা আকাশের নিচে রান্নাবান্না করত। ঐসময় বোদা পরগনায় সম্পূর্ণ পরিদর্শন করে ড. বুকানন, সেখানে কোন ইটের তৈরী পাঁকা ঘরবাড়ী দেখতে পাননি। অধিকাংশ ঘরবাড়ী ছিল কুড়েঘর। সেগুলো উলুখড় কাশবন দ্বারা আবৃত থাকত। সামান্য কিছু বাড়ীঘর বিন্যাখড় দ্বারা আবৃত বাড়ীর চার পাশে বাঁশ দিয়ে ঘেরা হতো। এ অঞ্চলের মুসলমানদের মসজিদ গুলো ছিল কুঁড়ে ঘরের।
অন্যান্য ধর্মের উপসনালয় গুলো কুঁড়েঘর হলেও কেবল মাত্র দুটি মন্দির তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল যা ইটের তৈরী। পরিধেয় বস্ত্রের ব্যাপারে যতটুকু জানা যায়, মেয়েরা সেলাইবিহীন একটি বস্ত্র খন্ড ব্যবহার করত। কেউ কেউ শাড়ী ব্যবহার করত। সাধারণত বাইরে বের না হলে ব্লাউজ পড়ার রেওয়াজ ছিলনা এ অঞ্চলে বরং বুকানি করে বস্ত্রখন্ড পরিধানের রেওয়াজ ছিল। পুরুষেরা ধুতি, লুঙ্গি, পিডান পরিধান করত। দরিদ্র জনগোষ্ঠী নেংটি পরিধান করত। পাদুকা পরার প্রচলন ছিলনা তবে ধনীক শ্রেণী কাঠের তৈরী খরম ব্যবহার করত। ১৯৩০ সালের দিকে এ অঞ্চলে রাজবংশী ক্ষত্রীয় সমিতি গড়ে তোলে, সমাজ সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে মেয়েদের বুকানি পরে যত্রতত্র যাতায়াত বন্ধ এবং পুরুষদের নেংটির পরিবর্তে বড় কাপড়, ধুতি, লুঙ্গি পরিধান করা জন্য প্রচার চালানো হয়। ফলে জলইপাইগুড়ি জেলার অন্যান্য অংশের ন্যায় এ অঞ্চলেও বুকুনী ও নেংটি পরার প্রচলন কমে যায়। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে কৃষি কাজ করা হতো, যারা হাল দিয়ে ও সেচের ব্যবস্থা করে চাষাবাদ করত তাদের বলা হতো বঙ্গ+আল=বঙ্গাল=বাঙ্গাল= বাঙ্গালী। তারা আবাদ করতো ধান, কাউন, পয়রা, আখ, আলু, আঙ্গালু, ধেমসী ইত্যাদি। ঢেঁকিছাটা চাউলের ভাত ছিল প্রধান খাদ্য।
এছাড়া কাউনের ভাত, পয়রার ছাতু, চাউল ভাজা ছিল এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য। ভাতের সঙ্গে মাছ–মাংসের প্রচলন ছিল সেই প্রাচীন কাল থেকেই। শোল, বোয়াল, কই, শিংগী, মাগুর, ভেদা, বালি, টেপা, বাইন, পঁয়া, গচি প্রভৃতি মাছ মানুষ পছন্দ করতো। হাঁস, মূরগী, ছাগল, ঘুঘু, কবুতর, পানি মাছ (কচ্ছপ), পাঠা, কাঁকড়া, কুচিয়া, বাইন মাছ প্রভৃতি মাংসের মধ্যে মানুষের পছন্দের ছিল । নিরামিষ ও শাকসবজির মধ্যে–বেগুন, কচু, কদু, কুমড়া, টমেটো, ছ্যাকা, কচুর ভর্তা, শুটকি, সিদঁল, ঢেকিয়া, পাটাশাক, লাফাশাক, কচুর মুড়া, প্যালকা ইত্যাদি। সরিষার তেল ও মহিষের দুধের ঘি–র প্রচলন ছিল প্রাচীন কাল থেকেই। নাস্তা হিসাবে দুধ, দই, চিড়া, মুড়ির প্রচলন ছিল। প্রাচীল কাল থেকেই এ এলাকার মানুষ পান, সুপারি নিজেরাও খেতো এবং অতিথিদের মধ্যে আপ্যায়ন করতো, যার প্রচলন এখনো পরিলক্ষিত। সেই সময় আখের প্রচুর আবাদ হতো মানুষ প্রচুর আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানিয়ে খেত। প্রাচীল কালে এ অঞ্চলে ডাল খাওয়ার কোন তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়নি।
প্রাচীন কাল থেকে এ অঞ্চলের মানুষ ছিল ধীরস্থীর ও শান্ত স্বভাবের। সকল মানুষই আরাম প্রিয় ছিল। সকালে ঘুম থেকে ওঠেই কৃষি কাজ সেরে স্নান করে আর কোন কাজ করতো না অধিকাংশ মানুষ। দুপুরের পরে নিজের বা কারো বৈঠকখানায় অথবা বড় কোন গাছের ছায়াতলে মাচা পেতে শুয়ে–বসে খোশগল্পগুজবে মেতে উঠতো এভাবে কেটে যেতো পড়ন্ত বিকেল । রাতে পুথি পড়ে, যাত্রা, রংপাঁচালী গান শুনে সময় কাটাতো । শীতকালে সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় আগুন পোহানো ছিল একটি পরিচিত দৃশ্য যা স্বল্প পরিসরে আজো বলবৎ আছে। চায়ের প্রচলনের কোন তথ্য নেই। তবে হুক্কা ও পাতার বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস ছিল অনেকের, বড়দের পাশাপাশি হুক্কাতে মুখ বসাতো ছোটরাও।
প্রাচীন কাল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সামাজিকতার ছাপ স্পষ্ট ছিল। গ্রামের অসুস্থ্য মানুষকে দেখতে যাওয়া, মৃত মানুষের চিতা ও জানাযায় অংশ নেওয়া ছিল সামাজিক রীতি। মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে কয়েকদিন যাবৎ রান্না বান্না হতো না। প্রতিবেশীরাই এই সময় খাবার সরবরাহ করত। যা আজো আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত আছে। এই জনপদের পর্দাপ্রথা খুব একটা ছিলনা বললেই চলে। উচ্চবিত্তের মহিলাদের মধ্যে মোটামুটি পর্দার প্রচলন চিল। গ্রামের দরিদ্র মহিলাগণ গ্রামের মধ্যেই মুক্ত ভাবে চলাফেরা করতেন। অবশ্য অপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে বের হতেন না, এবং কথা বলতে চাইতেন না। উচ্চবিত্তের হিন্দু মহিলারাও পর্দা মেনে চলতেন।
পরিবেশ:
প্রাচীন কাল হতে মানুষ গরু/ মহিষ দিয়ে হাল চাষ করতো এবং গরু/মহিষের গাড়ীতে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতো। বিগত তিন দশকে এ অঞ্চলের জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষির আমুল পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতি যেভাবে তার আগ্রাসী ছোঁয়ায় আমাদের পরিবেশকে ধ্বংস করছে, তার চেয়ে বেশী ধ্বংস করছি আমরা নিজেরাই। কিন্তু বিগত তিন দশকে কৃষি ক্ষেত্রে যে ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের নামে সার, বীজ, কীটনাশক, স্যালোমেশিন এবং পাওয়ার টিলারের ব্যবহার দেখা দিয়েছে, তা আমাদের গ্রামীন পরিবেশের দৃশ্যপট পুরোপুরি পাল্টে ফেলেছে। যা আমাদের জন্য উপকারের সাথে সাথে অপকারও বয়ে এনেছে। এছাড়া যেখানে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক নিবিড়, সেখানে মানুষ ও পরিবেশের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আমাদের উপর প্রকৃতি তার হিংসাত্মক ভাব পোষণ করছে। সৃষ্টি করেছে বন্যা, ভূমিকম্প, খড়ার ন্যায় ভয়াবহ দূর্যোগ। সর্বোপরি অন্য অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও শতভাগ সুস্থ্য পরিবেশের অভাব এ অঞ্চলে বিদ্যমান। ইউক্যালিপটাস গাছের আধিক্য সহ পরিবেশ বিনাশী তৎপরতা সঠিক সময়ে বৃষ্টি না হওয়া, অসময়ে খড়া, বৃষ্টি ইত্যাদি দূর্যোগ নেমে আসছে
বর্তমানে এ অঞ্চল প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাচ্ছে। কেঁচো, পাখি, মৌমাছি, কীট পতঙ্গসহ নানা কারনে পারছেনা তাদের স্বাভাবিক জীবন ধারণ করতে। এমনকি প্রজননের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে পারছে না বংশবিস্তার করতে। আজকে বৈশাখ মাস। গম কাটার পরে বোরো আবাদের শেষ ক্ষণ। গম কাটার পরে জমি খা খা করছে, তাকিয়ে আছে প্রকৃতির দিকে, তিন দশক আগেও কেঁচো সহযোগিতা করতো আবাদি জমি চাষে। অধিকাংশ জমিতে মাটি উপর থেকে নিচে, নীচ থেকে উপরে নিয়ে এসে মাটি নরম করতো। তাই কেঁচোকে প্রকৃতির লাঙ্গল বলা হয়। কারন কৃষক লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করতো, আর কেঁচো চাষের প্রাথমিক কাজটিতে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করতো। এক সময় বর্ষাকালে গ্রামের মানুষ কেঁচোকে মাছ ধরার টোপ হিসেবে ব্যবহার করে লাভবান হতো। এখন যেহেতু অপরিকল্পিত পুকুর/ডোবা নেই, তাই আর কেঁচোকে মাছ ধরার টোপ হিসেবে ব্যবহারের কথা ভাবে না মানুষ। আজকাল কেঁচো চোখে পড়ে না বললেই চলে।
এক সময় মৌমাছির বিচরণ ছিল এ অঞ্চলের সর্বত্র। বড় বড় মৌচাকসহ মৌমাছি দেখা যেত অভিজাত পরিবার গুলোতে ও বিভিন্ন বন–জঙ্গলে, আর সেই সব মধু সংগ্রহ করা হতো গ্রামীণ কায়দায়। সংগৃহীত মধুকে ব্যবহার করা হতো চিনি ও গুড়ের বদলে, এছাড়াও সর্দিকাশি ও জ্বরের ঔষধ হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। সামাজিক নানান আচার অনুষ্ঠানে যেমন– শিশু জন্মের পর পরই বয়োজ্যষ্ঠরা শিশুর মুখে মধু দিয়ে নতুন অতিথিকে বরণ করে নিতো। জন্মের সময় মধু মুখে দিলে সন্তান মিষ্টভাষী, শান্ত–ন¤্র–ভদ্র স্বভাবের হবে এ ধরনের একটা বিশ্বাস ছিল এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে। বর্তমানে মৌমাছির চাক দেখা যেন অমাবস্যার চাঁদ দেখার মত।
আগে নানান প্রজাতির পাখির বিচরণ ছিল এ অঞ্চলের সর্বত্রই। বিশেষকরে শীত কালে নানান প্রজাতির অতিথি পাখি এ অঞ্চলে দেখা যেত, কিন্তু এখন আর শীতের পাখি তেমন একটা দেখা যায় না। গত তিন দশক আগেও এ অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে বিচরণ ছিল শালিক, বক, চিল, ঘুঘু, কোকিল, মাছরাঙ্গা, ডাহুক, দোয়েল, কাক, চাতক, কবুতর, বুলবুলি, ময়না, টিয়া, শ্যামা, কাঠঠোকরা, ধনেশ, বাবুইসহ আরো অনেক প্রজাতির পাখি। কয়েক বছর আগেও শীতের সকালে কৃষি জমি চাষ করার সময় কৃষকের হালগরু ও লাঙ্গলের পিছনে পিছনে এক শ্রেণীর পাখি কিচির মিচির কণ্ঠে মুখরিত করে তুলতো পরিবেশ। যেন অনুপ্রেরণা যোগানের জন্য কৃষককে অনুসরণ করতো এসব পাখি। আর সেই দৃশ্য এ অঞ্চলের মানুষের কাছে হিমালয় পর্বতমালার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য অবলোকন করার চেয়েও কোন অংশে কম ছিল না। কিন্তু এখন আর সে দৃশ্য চোখে পড়ে না, কারণ আজকাল হারিয়ে যাচ্ছে পাখি, বদলে গেছে জমি চাষের ধরণ, জমিচাষে ব্যবহার হচ্ছে লাঙ্গল গরুর বদলে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি।
এক সময় বাঙ্গালীর ঐতিহ্য ছিল গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ। এক সময় বাড়ী পাহাড়াদার হিসেবে বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ছিল কুকুর। বিড়াল বাড়ীর শোভা বর্ধন করতো বাড়ীতে বাড়ীতে বিড়াল দেখা যেত। এখন আর এ দৃশ্য খুব কমই চোখে পড়ে।
কালক্রমে আমাদের এ অঞ্চলে জীবন মানে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিগত তিন দশকেও কোন জোতদারের ছেলে মেয়ের দুটো পরিধেয় বস্ত্র ছিলনা। একটা শার্ট কিংবা প্যান্ট বড় ভাই পরার পরে সেটা কেটে ছোট ভাই পরতো। ঈদ, পুজা পার্বন ছাড়া কাপড় কেনা কোন বিত্তশালীদেরও সম্ভব ছিল না। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা বিত্তবানরা দুবেলা ভাত খেতে পারে নি। চলাচলের জন্য বাইসাইকেল ছিল সর্বোচ্চ বাহন। কিন্তু আজকাল সেই সব পরিবারের প্রাইভেট কারে চলাফেরা করা অসম্ভব নয়।
শেষকথা:
সময়ের বিবর্তন ও প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রভাবিত করবে। প্রত্যাশা এটাই ঐতিহ্যকে ধারণ করে, প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। নতুন নির্মাণে আমরা যেন বোদার অতীতকে ভুলে না যাই। অতীতকে ধারণ করে গ্রহণ–বর্জনের বাস্তবতাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আশাকরি পুরাতনের সাথে নতুন প্রজন্মকে সাথে নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই উন্নত সংস্কৃতিসমৃদ্ধ বোদা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো- মোঃ এমরান আল আমিন, এম,এ (ঢাবি) এল,এল বি



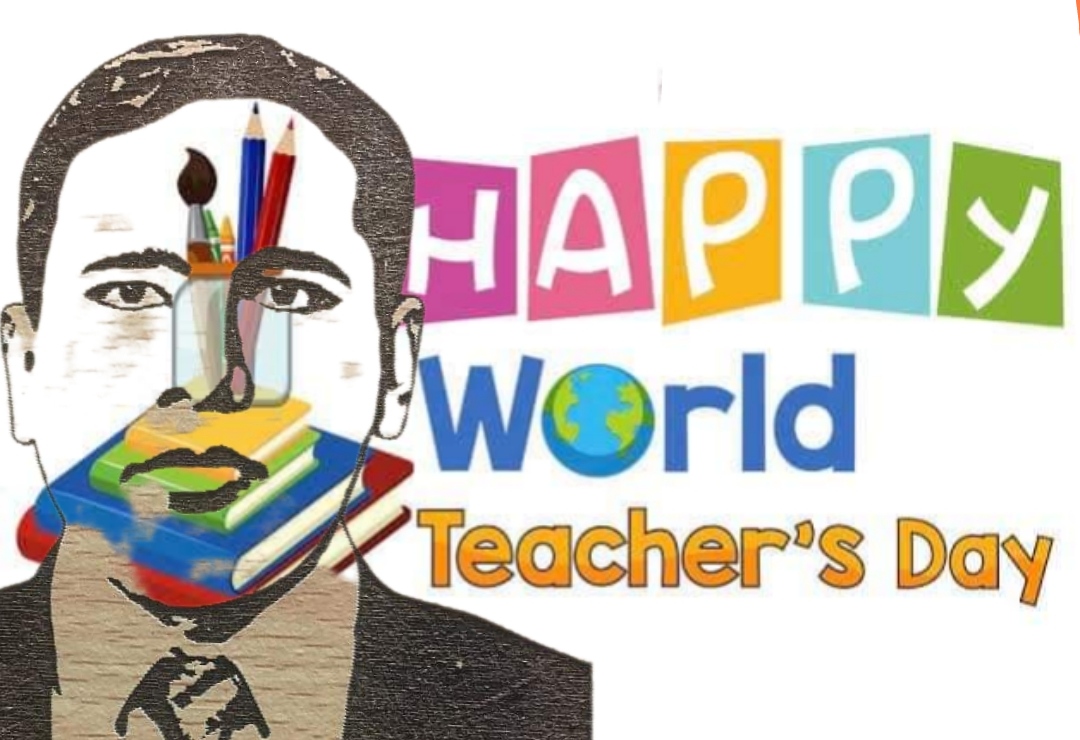


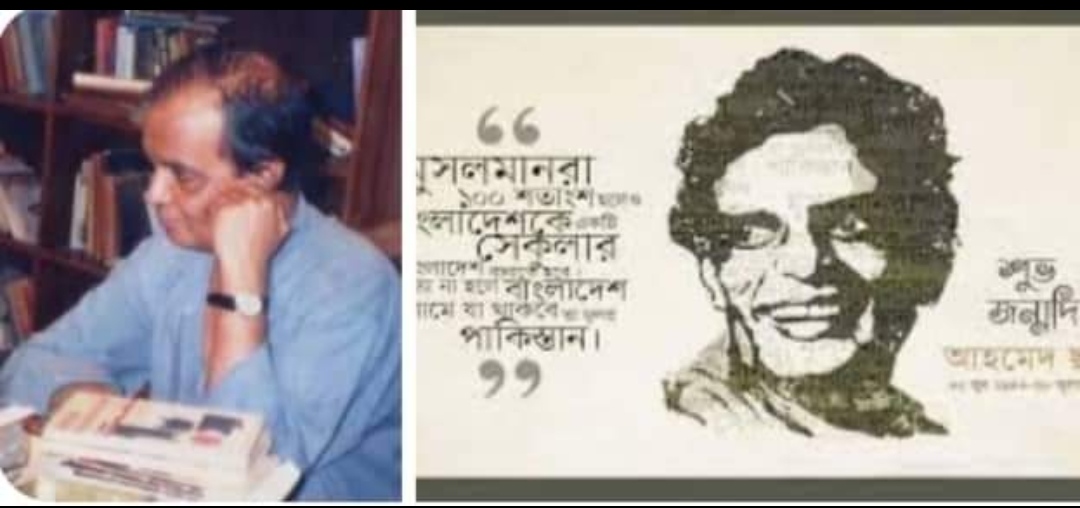
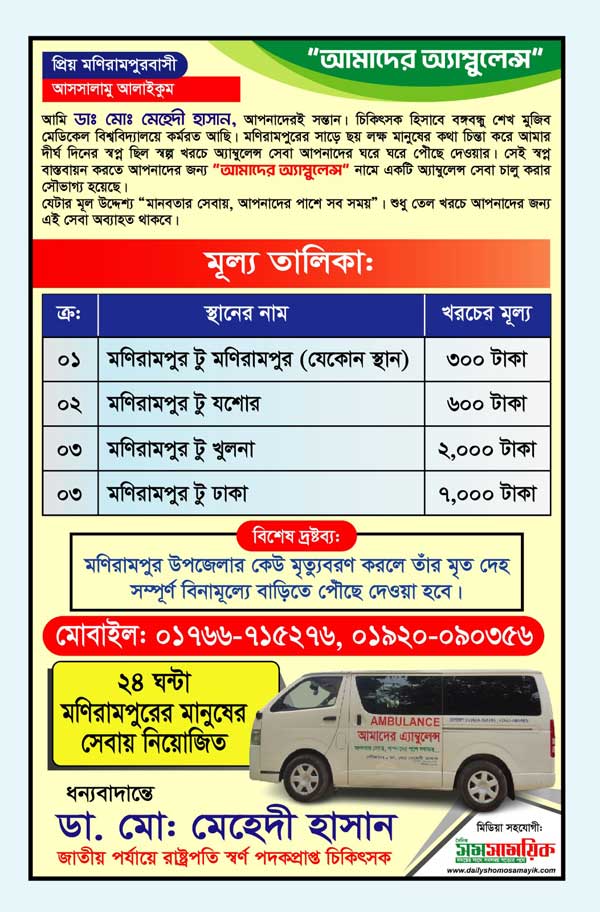





আপনার মূল্যবান মতামত দিন: